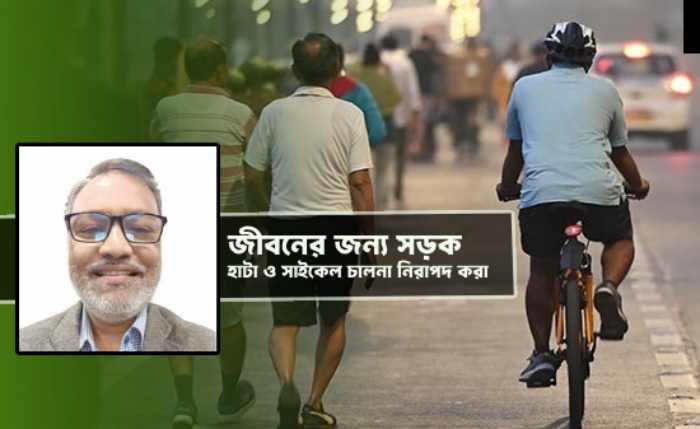এস এম আজাদ হোসেন: বিশ্বজুড়ে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সড়কে অকালমৃত্যু কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতি দু’বছর পর সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করে থাকে।এ বছরে ৮ম বৈশ্বিক সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ ১২ থেকে ১৮ মে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।‘এবার সপ্তাহটির প্রতিপাদ্য- ‘জীবনের জন্য সড়ক : হাঁটা ও সাইকেল চালানো নিরাপদ করা’ ।বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।
একটি দেশের উন্নয়ন কতটা মানবিক ও টেকসই-তা নির্ভর করে তার অবকাঠামো কতটা মানুষ-কেন্দ্রিক,পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ তার ওপর। বাংলাদেশের শহর ও গ্রামীণ সড়কব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে ‘যানমুখী’ পরিকল্পনার শিকার হয়ে মানুষকে পিছনে ফেলেছে। একদিকে আছে মোটরযানপ্রবণতা, অন্যদিকে হাটা ও সাইকেলচালকদের অবহেলা, যা তৈরি করেছে বৈষম্যমূলক, ঝুঁকিপূর্ণ ও বৈরী সড়ক বাস্তবতা। এখন সময় এসেছে এই ধারণার আমূল পরিবর্তনের।
জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী “Roads for Life” ক্যাম্পেইনের আওতায় “Safe Walking and Cycling” বা “নিরাপদ হাটা ও সাইকেল চালনা”-এই বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ এই ক্যাম্পেইনের সদস্য হলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটছে খুবই ধীরগতিতে। অথচ আমাদের শহর ও গ্রামাঞ্চলে এখনও বিশাল একটি জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা প্রতিদিন হেটে বা সাইকেল চালিয়ে চলাচল করেন। এসব মানুষই মূলত সমাজের শ্রমজীবী, শিক্ষার্থী, কৃষক, গৃহিণী কিংবা বয়স্ক নাগরিক-যারা সড়কে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে।
বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৮ থেকে ১০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন, যার মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই হাটা চলা বা সাইকেল চালনাকালে দুর্ঘটনার শিকার হন। সড়কে ফুটপাতের অভাব,বেপরোয়া যান চলাচল, জেব্রাক্রসিং ব্যবহারে অব্যবস্থা, ট্রাফিক আইনের অনুশীলনে গাফিলতি, এবং সর্বোপরি নগর পরিকল্পনায় সাইকেল ও পদচারি বান্ধব অবকাঠামোর অভাব-এসবই এই মৃত্যুগুলোর নেপথ্যে রয়েছে।
ঢাকার মতো মহানগরে যেখানে প্রতিদিন লাখো মানুষ হেঁটে চলাচল করেন, সেখানে ফুটপাত দখল হয়ে থাকে হকার,গাড়ির পার্কিং কিংবা নির্মাণ সামগ্রীর স্তূপে। এর ফলে সাধারণ পথচারীদের বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে মূল সড়কে হাঁটতে হয়। আরেকদিকে, সাইকেল চালকদের জন্য নির্ধারিত কোনো লেন নেই, নেই ট্রাফিক সুরক্ষা নির্দেশনা। ফলে তারা প্রতিনিয়ত ভ্যান, অটোরিকশা, বাস ও ব্যক্তিগত গাড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে থাকেন-যা এক ধরনের ‘রাস্তায় বাঁচা’র সংগ্রামে পরিণত হয়।
হাঁটা ও সাইকেল ব্যবহার শুধু যানজট বা সড়ক দুর্ঘটনা কমায় না; বরং এটি পরিবেশ সংরক্ষণ, জ্বালানি সাশ্রয়, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির দিক থেকেও অত্যন্ত কার্যকর। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত হাঁটে বা সাইকেল চালায় তাদের হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, মানসিক চাপ ও স্থূলতার ঝুঁকি অনেক কম। পাশাপাশি, একটি সাইকেল বা হাঁটা নির্ভর শহর বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকে।
বিশ্বের অনেক উন্নত শহর যেমন-কোপেনহেগেন, আমস্টারডাম, বার্সেলোনা কিংবা বার্লিন-এসব শহরে এখন যানবাহনের চেয়ে সাইকেলই বেশি চলে। শহরগুলোতে বিশাল সাইকেল লেন, পার্কিং, আলাদা ট্রাফিক সিগনাল ও আইন রয়েছে। এমনকি সাইকেল চালকদের জন্য আলাদা সামাজিক মর্যাদাও রয়েছে। অথচ আমাদের শহরে এখনও ‘সাইকেল’ যেন দরিদ্রের যান, যা আধুনিক নগরায়নের ভাষায় অপ্রাসঙ্গিক-এমন ভাবনা প্রচলিত।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, টেকসই পরিবহন নীতিমালা এবং সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনায় হাঁটা ও সাইকেলবান্ধব অবকাঠামোর কথা বলা হলেও বাস্তব বাস্তবায়নে দেখা যায় ঘাটতি। ঢাকায় কিছু এলাকায় সাইকেল লেন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা টেকেনি, কারণ পরিকল্পনা ছিল অস্থায়ী ও লোকদেখানো। এসব লেন দখল হয়ে যায় পার্কিং, ফুটপাত বা দোকানদারদের কবলে।
বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে সাইকেলকে উৎসাহিত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন আইনি ও অবকাঠামোগত নিশ্চয়তা। সড়কে হাঁটা ও সাইকেল চালানোকে অবশ্যই নাগরিক অধিকার হিসেবে গণ্য করতে হবে। এর জন্য চাই:
১) প্রতিটি নগর পরিকল্পনায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত সড়কপথ নির্ধারিত হতে হবে শুধু হাঁটা ও সাইকেল চালনার জন্য।
২) ফুটপাত মুক্ত রাখতে হবে কঠোর অভিযান,হকার পুনর্বাসন নীতি অনুসরণ করে।
৩) সাইকেল চালকদের জন্য আলাদা লেন,পার্কিং ব্যবস্থা এবং রাতের জন্য আলোসজ্জা নিশ্চিত করতে হবে।
৪) স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাইকেল চালনা উৎসাহিত করতে বিশেষ সাইকেল পথ তৈরি ও সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।
৫) সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারী বা সাইকেল আরোহীর মৃত্যু ঘটলে, আইন অনুযায়ী বিচার ও ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
৬) ট্রাফিক পুলিশের প্রশিক্ষণ দিতে হবে সাইকেল ও হাটাচলার অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার জন্য।
আমাদের নগর উন্নয়নের গতিপথ এখনো মোটরযানের চাহিদা পূরণের দিকে মোড় নিচ্ছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল, ফ্লাইওভার-এসব ব্যয়বহুল অবকাঠামো শহরের সমস্যার মূল শিকড়ে আঘাত না করে বরং সমস্যাগুলোর চারপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো উন্নয়নের অংশ হতে পারে, তবে সমাধান নয়। একটি উন্নত শহর সে, যেখানে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা গৃহিণী নিরাপদে হাঁটতে পারে। যেখানে তরুণ ছাত্রটি সকালে নিশ্চিন্তে সাইকেল চালিয়ে ক্লাসে যেতে পারে। যদি আমরা এই ভবিষ্যতের দিকে না যাই, তাহলে শহর হবে কংক্রিট আর কনজেশনের জঙ্গল।
হাঁটা ও সাইকেল ব্যবহার শুধু অবকাঠামোর বিষয় নয়, এটি একটি সংস্কৃতির বিষয়। সেই সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, সামাজিক আন্দোলন, এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। স্কুলে ‘সাইকেল দিবস’, পাড়ায় ‘পথচারী র্যালি’, স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে ‘হাঁটা সপ্তাহ’ আয়োজন-এসবই এই সচেতনতা তৈরির কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।
আমরা যখন বলি, “সড়ক যেন জীবন রক্ষার পথ হয়”, তখন তার অর্থ শুধু দুর্ঘটনার ভয় কমানো নয়; বরং তার অর্থ-একটি সমাজ কতটা মানবিক, কতটা সমতার পক্ষে, এবং কতটা পরিবেশবান্ধব।
বাংলাদেশ একটি নবজাগরণে দাঁড়িয়ে আছে-যেখানে উন্নয়নকে আর কেবল গড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না, বরং বাঁচিয়ে রাখার নীতিও জরুরি। হাঁটা ও সাইকেল চালনা সেই বাঁচিয়ে রাখার পথের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আমাদের শহরগুলোকে ফিরিয়ে দিতে হবে পথচারীদের হাতে, ফিরিয়ে দিতে হবে সাইকেলের স্বাভাবিক গতি, ফিরিয়ে দিতে হবে একটি নিরাপদ, প্রশস্ত, সবজায়গায় মানুষের জন্য তৈরি সড়কব্যবস্থা। কারণ রাস্তাগুলো কেবল যানবাহনের নয়-এগুলো মানুষের জন্য।
লেখকঃ কলামিস্ট,মহাসচিব-নিরাপদ সড়ক চাই।